ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সকল তথ্যাবলী
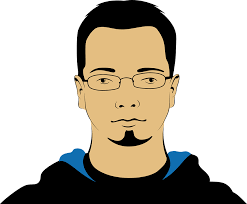
- প্রকাশিত : শুক্রবার, ১৩ মে, ২০২২
- ১১১২ বার পঠিত

অবস্থান:
ভূরুঙ্গামারী উপজেলাটি কুড়িগ্রাম জেলার উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত। ২৬°২০´ থেকে ২৬°১৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৬´ থেকে ৮৯°৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
তিন দিকে ভারত বেষ্টিত এই উপজেলার পশ্চিমে- পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানা।
উত্তরে- কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানা, পূর্বে- আসামের ধুবরী জেলার গোলকগঞ্জ থানা, দক্ষিণে- কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানা।
আয়তনঃ
৯১.২২ বর্গমাইল। ২৩১.৭০ বর্গকিলোমিটার। ৫৮,৩৮১.২ একর।
প্রশাসনিক এলাকা:
এটি কুড়িগ্রাম -১ সংসদীয় এলাকার অধীন; যা নাগেশ্বরী এবং ভূরুঙ্গামারী নিয়ে গঠিত। ভূরুঙ্গামারী উপজেলাতে ১২৮টি গ্রাম, ৭০টি মৌজা, ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।
ইউনিয়ন গুলি হলঃ
১.পাথরডুবী ইউনিয়ন
জিও কোড-৭৬
আয়তন- ৬৩৬৩ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ৯৯৪২জন,পুরুষ- ৯৭০২জন
২.শিলখুড়ি ইউনিয়ন
জিও কোড-৮৫
আয়তন- ৬৭৩২ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা-৯৫৯২জন,পুরুষ- ৯১৩৪জন
৩. তিলাই ইউনিয়ন:
জিও কোড-৯৫
আয়তন- ৪৭৮৫ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ৭০৩৯জন,পুরুষ- ৬৮০৫জন
৪. পাইকেরছড়া ইউনিয়ন:
জিও কোড-৬৬
আয়তন- ৬৩২০ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ১০৯৫৭জন,পুরুষ- ১০৯৪০জন
৫.ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়ন:
জিও কোড-১৯
আয়তন- ৭১৬২ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ১৮৬৬৫জন,পুরুষ- ১৯১৬৯জন
৬.জয়মনিরহাট ইউনিয়ন:
জিও কোড-৫৭
আয়তন- ৪৩৭২ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ৭৮৬৬জন,পুরুষ- ৭৮৪২জন
৭.আন্ধারীঝাড় ইউনিয়ন:
জিও কোড-০৯
আয়তন-৬৫২৩ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা-৯৬০৯জন,পুরুষ– ৯৫৮২জন
৮.বলদিয়া ইউনিয়ন:
জিও কোড-২৮
আয়তন- ৬১২৬ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ১১০১৭জন,পুরুষ- ১০৪১৬জন
৯.চরভূরুঙ্গামারী ইউনিয়ন:
জিও কোড- ৪৭
আয়তন- ৪৬০২ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ৬৩২০জন,পুরুষ- ৬২০১জন
১০. বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়ন:
জিও কোড-৩৮
আয়তন- ৫৩৩১ একর
লোক সংখ্যা-মহিলা- ৮২৮৮জন,পুরুষ- ৭৯৮৪জন
নাম করণের ইতিহাস: ভূরুঙ্গা মাছের প্রাচুর্য থেকে এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে ভূরুঙ্গামারী। লোকজন দল বেধে মাছ মারতে যাওয়ার সময় একে অপরকে আহ্বান করত ‘চল ভূরুঙ্গা মারতে যাই’। এভাবে ভূরুঙ্গামারী নামটি প্রচলিত হয়েছে। অভিন্ন বাংলায় ভূরুঙ্গামারী কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বে ভূরুঙ্গামারী কোচ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। গয়াবাড়ি স্টেট নামে ছিল।ভূরুঙ্গামারী-সোনাহাট রোডটি মিলিটারী রোড নামে পরিচিত।
কথিত আছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তাটি তৈরি করেন। রাস্তাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসামের মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাটি বাগভান্ডার বিডিআর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ১৯১৫ সালের পূর্বে ভূরুঙ্গামারী নাগেশ্বরী থানার অধীনে ছিল। এ সময় ভূরুঙ্গামারীতে ফুলকুমার নামে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। ১৯১৫ সালে ভূরুঙ্গামারী পৃথক থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ফুলকুমার নামক পুলিশ ফাঁড়িটি থানা সদরে স্থানান্তরিত হয়।
বঙ্গসোনাহাট বিডিআর ক্যাম্পের পূর্ব দক্ষিণ দিকে একটি পুরোনো তালগাছ এখনো অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে।
১৯৬৬ সালে দেওয়ানের খামার নামক স্থানে ভূরুঙ্গামারী শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভূরুঙ্গামারীকে ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে মানউন্নীত থানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
জনসংখ্যা:
২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে
জনসংখ্যা ২,৩১,৫৭৪ জন।
পুরুষ: ১,১৩,৫০২ জন।
মহিলা: ১,১৮,০৩৬ জন।
মুসলিম জনসংখ্যাঃ ২,২৭,৫৭৪ জন।
হিন্দুঃ ৩,৯৪৫ জন।
বৌদ্ধঃ ১১ জন।
খ্রিষ্টানঃ ১৫ জন।
সময় অঞ্চল: বিএসটি (ইউটিসি +৬)
পোস্ট কোড: ৫৬৭০
সংসদীয় আসন: কুড়িগ্রাম-১
প্রতিষ্ঠা কাল: ১৯১৫ সাল
উপজেলায় রূপান্তর : ১৯৮৩ সালের ১০ এপ্রিল
আয়তন: ২৩১.৭০ বর্গ কিমি (৮৯.৪৬ বর্গমাইল)
জনসংখ্যা ঘনত্ব: ১০০০/ বর্গ কিমি(২৬০০/বর্গমাইল)
শিক্ষা ব্যবস্থা:
শিক্ষার হার: ৭২.৬% (২০১৭)
পুরুষ:৭৯.০৮%
মহিলা: ৬৫.৪০%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :
- কলেজ -৫টি।সরকারি ১টি
- কারিগরি (বিএম) কলেজ – ৪টি
- উচ্চ বিদ্যালয় – ২৩টি। সরকারি ১টি
- বালিকা বিদ্যালয়- ৭টি।
- জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় -২টি।
- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় – ১১১টি।
- ফাজিল মাদ্রাসা – ২টি।
- আলিম মাদ্রাসা – ২টি।
- দাখিল মাদ্রাসা- ১৫টি।
- ইবতেদায়ী মাদ্রাসা- ১৯টি
উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভুরুঙ্গামারী ডিগ্রি কলেজ (১৯৬৭), ভুরুঙ্গামারী মহিলা ডিগ্রি কলেজ (১৯৯৪),সোনাহাট মহাবিদ্যালয়(১৯৯৯),ভুরুঙ্গামারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৫), পাটেশ্বরী বরকতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫০), থানাঘাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬১), ধামেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৫০), ভুরুঙ্গামারী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাউশমারী সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৩৮), ভুরুঙ্গামারী সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৪৮)।
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য:
- উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ টি
- উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৪টি
- পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১০টি
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক ৪২টি
- বেসরকারি ক্লিনিক ৭টি
- ডায়াগনস্টিক সেন্টার ১টি।
আয়ের প্রধান উৎস :
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৭৫.২%, অকৃষি শ্রমিক ৪.১৫%, শিল্প ০.৪%, ব্যবসা ৮.০৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১.৪৮%, চাকরি ২.৯৯%, নির্মাণ ০.৪৪%, ধর্মীয় সেবা ০.১১%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.৩% এবং অন্যান্য ৬.৮৭%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৪.৪৫%, ভূমিহীন ৪৫.৫৫%। শহরে ৪৪.২৩% এবং গ্রামে ৫৫.৭৮% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।
ভূরুঙ্গামারী উপজেলার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৬,৯০০ একর। অত্র উপজেলায় ফসল ধান, গম, পাট, রাই-সরিষা, আলু, ইক্ষু, ভুট্টা ও সুপারি ইত্যাদির ব্যবসা মোটামুটি প্রচলিত। রফতানী যোগ্য পন্য বলতে ধান, চাল, পাট,আলু ও সুপারি। ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে ধান, চাল, পাট,মাছ,সুপারি ও সবজি।
ছাড়াও গরু ও অন্যান্য দ্রব্যাদীর ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে থাকে।এছাড়াও অত্র উপজেলায় নদী পথে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে অনেক সময় মালামাল ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।
প্রধান কৃষি ফসল:
ধান, পাট, আলু, গম, আখ,সুপারি, বাঁশ, শাকসবজি। বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি চীনা, বিলুপ্ত ফসল আউশ ধান, অড়হর।প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, সুপারি, কামরাঙা, জলপাই, পেয়ারা, জাম, চালতা, জামরুল, লটকন।
প্রধান অর্থকরী ফসল:
ধান,সুপারি,পাট ও মৌসুমী সবজি।
বানিজ্যিক ভাবে গরু মোটাতাজাকরণ,দুগ্ধ উৎপাদন খামার,মুরগী খামার ও মাছ চাষে প্রচুর জনগোষ্ঠী জড়িয়ে রয়েছে। উপজেলার অধিকাংশ বাড়িতে দেশীয় জাতের গরু,ছাগল,ভেড়া,হাঁস,মুরগী ও কবুতর পালন করে থাকে। এসব উপজেলার অর্থনীতি উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখে।
মৃৎ শিল্পঃ
মাটি আর মানুষ আমাদের বড় সম্পদ। এ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার মৃৎশিল্পে। ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার এঁটেল মাটির তৈজসপত্র দ্রব্যাধার পুতুল ও দেবদেবীর বিগ্রহ দেখতে সুন্দর,কাজে টেকসই।গবাদি পশুর সম্মুখে যে পাত্রে খাওয়া দেওয়া হয় তার নাম চাড়ি। ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এটি তৈরি হয়। এছাড়া মটকি বা কোলা বা বিশাল বপু পাতিল তৈরি হয় ভূরুঙ্গামারীর বিভিন্ন কুমার পাড়ায়।
মাটির তৈজসপত্র, সানকি, হাড়ি, সরা, বাটি, পিঠা তৈরির ছিদ্রযুক্ত পাতিল,কোলা,গুড়ের মটকি প্রভৃতি ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার কুমারদের অনবদ্য সৃষ্টি।এসব মাটির জিনিসপত্র সাধারণত বিভিন্ন হাট-বাজার ও মেলায় বিক্রি হয়। ফেরি করেও বিক্রি করা হয়। ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার কুমারদের মধ্যে অনেকে প্রতিমা নির্মাণে সিদ্ধহস্ত।
এছাড়া ঘোড়া, গরু, বাঘ, হাতি, কুকুর, মাছ, আম, কাঁঠালসহ নানা ধরনের খেলনা শিশুদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়। এই শিল্পের উন্নয়নে আজও কিছু করা হয়নি। আদিমকালের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে কুমাররা এখনো কাজ করে যাচ্ছেন।
বাঁশ ও বেত শিল্পঃ
ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার বাঁশ ও বেতশিল্পেরও রয়েছে একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস। বাঁশ দিয়ে শুধু বাঁশি তৈরি হয়নি। এদিয়ে তৈরি হয়েছে নানাবিধ উপকরণ। ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার বেতঝোপ থেকে বেত কেটে এনে হাতের গুণে তৈরি করা হয় নানা প্রকার ব্যবহারযোগ্য জিনিস। বেতের ডালিয়া, ধান চাউলের বেড় ও তিল তিসি, সরিষা রাখার ছোট বড় ডুলি। বাটখারা প্রচলনের পূর্বে এক সেরি, পাঁচসেরিসহ সকল প্মুরকার মাপনি পাত্র (যা স্থানীয় ভাবে টালা বলা হতো) মানকা বা ধামার ব্যবহার ছিল।
এসব এখনো গ্রামাঞ্চলে রোন্নার চাউল মাপতে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের চটি দিয়ে তৈরি হয় ডালি, চাটাই, ধাড়ি, কাইত্যা, বেড়, ডুলি, ঘরের বেড়া। এছাড়াও টুকরি, ঝাকা, কূলা চালনি, খালই, তালাই, প্রভৃতি।
আজো গ্রাম বাংলায় কৃষিকাজ করার জন্য কৃষকের মাথায় মাথাইল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার বিপুল সংখ্যক নারীপুরুষ বাঁশজাত সামগ্রী তৈরির কাজে নিয়োজিত আছেন।
ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার পাট বেতের সাহায্যে চমৎকার হস্তশিল্প শীতল পাটি তৈরি হয়। বুনন কৌশলে ও কাজের দক্ষতায় যে কোন সাধারণ পাটিতেও ফুটিয়ে তোলা হয় জ্যামিতিক নকশা। এছাড়া জীবজন্তু, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, ফুল, লতাপাতা, মিনার, মসজিদ, নৌকা, পালকী প্রভৃতি ফুটে উঠে শীতল পাটির বুননের মাধ্যমে।
তারা সাধারণ ও শীতল পাটি বুনে থাকে। ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার গ্রামাঞ্চলে ৫/৭ ফুট উঁচু একপ্রকার গাছের ছাল দিলে পাটি তৈরি করা হয়। গরমের সময় কারুকার্যময় শীতল পাটি বিছানায় ব্যবহার করলে শরীর ঠান্ডা হয়।
কাঠ শিল্প:
প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই সূত্রধর বা ছুতার আমাদের গ্রাম জীবনের প্রয়োজনে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি সরঞ্জাম যেমন, লাঙ্গল, ঈষ, মই, আচড়া, ইচামুগর, গরুর গাড়ি, গৃহনির্মাণ ও নৌ-নির্মাণে সূত্রধররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
সামাজিক দাবি মিটানোই ভূরুঙ্গামারীর উপজেলারর সূত্রধরদের কাজ। খাট, পালঙ্ক, বারকোশ, পিঁড়ি, টুল, জলচৌকি থেকে শুরু করে আধুনিক টেবিল চেয়ার শোকেস, আলমিরা প্রভৃতি তৈরিতেও ভূরুঙ্গামারীর সূত্রধররা দক্ষতার সাথে কাজ করছে।
উপজেলার নদী ও খালের তীরে অনেক এলাকায় নৌকা তৈরি করা হয়। সাধারণ ধরনের নৌকায় করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দ্রব্যাদির ব্যবসা বাণিজ্য চলে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার নৌকাও তৈরি হয়।
ঘানি শিল্পঃ
ভূরুঙ্গামারীর উপজেলার তেলি বা কলু সম্প্রদায় তিল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ ভেঙ্গে প্রস্তুত করে তৈল। ঘানি ঘোরাবার জন্য চোখ বাঁধা বলদ ব্যবহার করা হয়। কলের ঘানির সাথে বলদের ঘানি পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারছে না বলে কলুরা আজ পেশাচ্যুত হয়ে পড়েছে। এই শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে।
তাছাড়া মুচি গরুর চামড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করে। এদের মধ্যে অনেকে জুতাও তৈরি করে আসছে। এদের অনেকেই ঢাক, ঢোল, তবল, ডুগি প্রভৃতি তৈরি করে থাকে। এই মুচিদের সংগঠিত করতে পারলে চর্মশিল্পের অনেক উন্নতি বিধান করা সম্ভব।
তাঁত শিল্প:পাকিস্তান আমলে এখানে একটি তাঁতি পাড়া ছিল।তাঁতির লুঙ্গি, গামছা এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করত।তাঁতীরা জোলা নামে পরিচিত ছিল।তাদের বংশধররা এখন অন্য পেশায় জড়িত।জোলাটারী এখনো কালের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে।এখনো এখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষ টাঙ্গাইলের তাঁত ও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন।
প্রয়োজন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দরকার কাচামাল, ঋণ এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে টাঙ্গাইলে কাজ না করে ভূরুঙ্গামারীতে এসব কাজ করতে এছাড়া ভূরুঙ্গামারী উপজেলার গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে এক সময় ঢেঁকির প্রচলন ছিল।
এসব কুটির শিল্পের বিকাশ বহু বছর পূর্ব থেকেই। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক এখানে এসে বসবাস করে বংশানুক্রমিকভাবে এসব শিল্পের কাজ শুরু করেছে। কুটিরশিল্প ছিল ঐতিহ্যবাহী এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত। এই শিল্পের এখনো প্রচুর সম্ভাবনী রয়েছে- শুধুমাত্র উদ্যোগের অভাব।
ভূরুঙ্গামারীর উপজেলারবাসীর উন্নয়নে তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্প খাত যাতে নতুন উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে বিষয়ে প্রতিটি সচেতন মানুষ ও সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।
যোগাযোগ ব্যবস্থা:
ঢাকাসহ সারা দেশের সাথে ভুরুঙ্গামারী উপজেলার খুব ভাল সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।তবে রেলপথ নেই। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের লালমনিরহাট থেকে ভারতের মনিপুর রাজ্যে ইংরেজদের সৈন্য ও রসদ স্থানান্তরের সুবিধার্থে রেলপথ স্থাপন করে।এই রেলপথ বাংলাদেশের লালমনির হাট থেকে ভারতের অভ্যন্তর দিয়ে সিংঝাড় দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে পুনরায় ভারতের আসাম রাজ্যে প্রবেশ করে।
ভূরুঙ্গামারী ও লালমনির হাটের মধ্যবর্তী স্থানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হওয়ায় দেশ বিভক্তির পর রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়। রেল লাইনটি এখন পরিত্যাক্ত অবস্থায় রয়েছে।
- জেলা সদর হতে দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক পথে): ৪০ কিলোমিটার
- জেলা সদর হতে সোনাহাট স্থল বন্দরের দূরত্ব (সড়ক পথে): ৫২ কিলোমিটার
- উপজেলা সদর হতে স্থল বন্দরের দূরত্ব (সড়ক পথে): ১২ কিলোমিটার
-
উপজেলা সদর হতে প্রস্তাবিত বর্ডার হাটের দূরত্ব (সড়ক পথে): ০৩ কিলোমিটার
-
ভুরুঙ্গামারী হতে ঢাকার দূরত্ব (সড়ক পথে) : ৩৯৩ কিলোমিটার
-
মোট সড়ক পথ: ৪১৭.৯৭ কিলোমিটার
-
পাঁকা রাস্তা: ৮২.৫৬ কিলোমিটার
-
কাঁচা রাস্তা: ৩৩৫.৪১ কিলোমিটার
-
ব্রীজ কালভার্টের সংখ্যাঃ ৩১২ টি
যানবাহন: বাস, মোটর বাইক, বিদ্যূৎ চালিত রিক্সা, সাইকেল, অটো রিক্সা, নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, বিলুপ্তপ্রায় পা চালিত রিক্সা, গরু ও মহিষের গাড়ি, বিলুপ্ত সনাতন বাহন পাল্কি।
প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব:
শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজসেবা ও সাহিত্য চর্চাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের পরিচয় সংক্ষেপে তুল ধরা হল:
শামসুল হক চৌধুরী:
চর বলদিয়া গ্রামে ১৯৩৬ সালের ৩০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ভূরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ পাশ করেন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।
তার বাবার ইচ্ছা ছিল তাকে ডাক্তার বানানোর কিন্তু তিনি বাস্তব জীবনে ডাক্তার না হয়ে হয়েছিলেন রাজনীতিবিদ। প্রথম জীবনে তিনি ভূরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।
তিনি রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়ানোর পর তার শিক্ষক আব্দুল হকের পরামর্শক্রমে পারিবারিক উপাধি মন্ডলের পরিবর্তে তার নামের সাথে চৌধুরী উপাধি ব্যবহার করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ক্রীড়া সংগঠক ও সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি এম.পি নির্বাচিত হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ছিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালেও তিনি পুনরায় এমপি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ভূরুঙ্গামারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
তিনি ভূরুঙ্গামারী ডিগ্রী কলেজসহ বেশকিছু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ২০০৮ সালের ৭ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
মোঃ কফিলুর রহমান:
১৯৪২ সালে দেওয়ানেরখামার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। পেশাগত জীবনে তিনি ব্যবসায়ী হলেও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি নেহাল উদ্দীন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।
অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক:
১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বহালগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮২ সালে সহকারি অধ্যাপক, ১৯৯১ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯৭ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। দীর্ঘ চাকরি জীবনে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯৭৮ সালে জনসংখ্যা ও শিক্ষা ওয়ার্কশপ, ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন ওয়ার্কশপ এবং ২০০১ সালে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সনদ লাভ করেন। তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত থেকে কুড়িগ্রাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।
ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব ও সংগঠন ‘বঙ্গ’ বাঙ্গালা, বাংলাদেশ: আন্দোলন-সংগ্রাম-রাজনীতি-নির্বাচন প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার পদেও কর্মরত ছিলেন।
জয়নাল আবেদীন ভান্ডারী:
কোচবিহার জেলার মারগঞ্জ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি একাধারে কবি ও সম্পাদক ছিলেন। জয়নাল আবেদীন কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার মারগঞ্জ থেকে এসে কুড়িগ্রাম জেলার সদয় উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নে বসবাস শুরু করেন।
এরপর বেলগাছা থেকে তিনি ভূরুঙ্গামারীর নলেয়া নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। একটি কবিতায়
তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,
“আমি ভান্ডারী ছাপাখানা হয়ে এসেছি
নলেয়ার এই পল্লী কুঠিরে বসেছি।
রাজা নই তাই রাজেন্দ্র নাম ধরি না
আমি ভান্ডারী মানুষের খেদমত ছাড়া থাকি না।”
পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে তার সম্পাদনায় মাসিক বার্তাবহ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। প্রেসের কাজের চাপ কম থাকলে পত্রিকার কলেবরে বৃদ্ধি পেত। কাজের চাপ বেশি থাকলে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হত।
জয়নাল আবেদীন ১২টি কাব্য গ্রন্থ লিখেছেন। প্রেম ফুল, প্রেম ফল, প্রেম তরী, প্রেম বৈঠা, প্রেম গাছ, প্রেম পাতা প্রভৃতি তার অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। বার্তাবহের কভার পেজে তার অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা ছাপানো হত। ১৯৯৩ সালের ১০ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন
আব্দুল হাই শিকদার :
১৯৫৭ সালের ১ জানুয়ারি ছাট গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ের কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কবিতা, গল্প ও শিশুসাহিত্যে তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।
এ পর্যন্ত তার আশিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শেকড় সন্ধানী কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।
এছাড়া তিনি একজন ভাল উপস্থাপক ও প্রামাণ্য চিত্র নির্মাতা।কর্ম জীবনে তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালকসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।
তিনি বাংলাদেশের প্রথম নিয়মিত মাসিত সাহিত্য পত্রিকা ‘এখন’ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি তার প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আশি লক্ষ ভোর, আগুন, আমার ভাই, কবি তীর্থ চুরুলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
এ. এস. এম মহিউদ্দিন আলমগীরঃ
১৯৪৮ সালের ১ নভেম্বর উলিপুর থানার দড়িচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে ভূরুঙ্গামারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মৌলভী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি একই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কবি ও ইসলামী চিন্তাবিদ। শতাব্দীর অভিশাপ, কেয়ামতের বিভীষিকা, ভোরের পাখি, রক্ষ সিন্দুর বেলাবূীম প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
তৈয়বুর রহমানঃ
১৯৬৩ সালে পাটেশ্বরীতে জন্মগ্রহণ করেন।এলএলবি পাশ করলেও আইন পেশায় না জড়িয়ে তিনি প্রাইমারী শিক্ষকতা করছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের তালিকাভূক্ত গীতিকার ও নাট্যকার। জীবন যুদ্ধ, শিক্ষার আলো, যুদ্ধের নয় মাস প্রর্ভৃতি তার উল্লেখযোগ্য নাটক।তিনি বর্ণালী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।২০২০সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
খেলাধুলা: প্রাচীনকাল থেকেই ভূরুঙ্গামারী উপজেলার জনগোষ্ঠী ক্রীড়ামোদী। এখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বর্তমানে ক্রিকেট ও ফুটবলের আধিপত্য দেখাগেলেও অন্যান্য খেলাও পিছিয়ে নেই। ভূরুঙ্গামারীতে বেশ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। এর মধ্যে ভূরুঙ্গামারী ডিগ্রী কলেজ মাঠ, ভূরুঙ্গামারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ,পাটেশ্বরী বরকতীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ দু’টি উল্লেখযোগ্য।
প্রতি বছর এ দু’টি মাঠে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় ভাবে ফুটবল ও ক্রিক্রেট লীগ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা পাটেশ্বরী বরকতীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিবছর আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল কাপ ও সোনামিয়া প্রিমিয়াম ক্রিকেট লীগ অনুষ্ঠিত হয়।
এছাড়া ব্রিটিশ আমলে গাগলার শ্যামাসুন্দরী স্টেটের নায়েব রঞ্জিত কুমার সরকার ভূরুঙ্গামারীতে ‘শ্যামা সুন্দরী সিল্ড’ নামে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন।
সে সময় বৃহত্তর রংপুরের ফুটবল টিম, গৌরিপুরের মহারাজার ফুটবল টিম এবং কলকাতা, গৌহাটি, ধুবড়িসহ আরো অনেক জায়গা থেকে ফুটবল টিম ভূরুঙ্গামারীতে খেলতে আসত। ১৯৫২ সালের পর এই ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।
এছাড়াও ব্রিটিশ আমলে পাইকের ছড়ার ফুটানীর বাজার ও পাটেশ্বরী রেল ইস্টিসনের মধ্যবর্তী স্থানে (বর্তমান হ্যালিপ্যাড ও এর পূর্ব দিকে) একটি বিরাট ফুটবল খেলার মাঠ ছিল। সেখানে প্রতিবছর ”সোনা ও কোনা সিল্ড” নামে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হতো। সে সময় বৃহত্তর রংপুরের ফুটবল টিম, গৌরিপুরের মহারাজার ফুটবল টিম এবং কলকাতা, গৌহাটি, ধুবড়ি, গ্লোবগঞ্জসহ আরো অনেক জায়গা থেকে ফুটবল টিম খেলতে আসত।
লাঠি খেলা,হা-ডু-ডু, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার প্রচলন রয়েছে। লাঠি খেলার জন্য পাইকের ছড়ার কালীর হাট, আন্ধারীঝাড়ের মধ্যচরের লাঠিয়ালদের ব্যাপক জনপ্রিয়।
সংস্কৃতি:
আদিকাল নাটক, গান-বাজনায় ভূরুঙ্গামারী জাঁকজমক ছিল। সোনাহাট রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন স্থানে পাশাপাশি দু’টি সিনেমা হল ছিল। দু’টি হলের মধ্যে একটি ছিল শ্রীশ চন্দ্র নন্দীর এবং অন্যটি ছিল আসামের গৌরিপুরের জমিদারের। দুর্গা পুজা উপলক্ষে সোনাহাটে মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলায় সার্কাস এবং যাত্রাগানসহ বিভিন্ন রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত। মেলা কতদিন স্থায়ী হবে এ নিয়ে দুই জমিদারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত।
এ ছাড়া উপজেলার পাইকের ছড়া ইউনিয়্নের গায়ক ও গিদালদের জনপ্রিয়তা প্রচুর ছিল।উপজেলার বাহিরেও এদের নাম ডাক ছিল।
সরাজ গান, ধুয়া গান(লেটো গান), জঙ্গনামা, পদ্মপুরান, কুশান গান, কবিয়াল গান ও পুথি পাঠের খুবই প্রচলন ছিল।এ সব গানের গায়ক, বাদক, দোহার বেশী ভাগই পাইকের ছড়া ইউনিয়নের ছিল্।
ঝরু গিদাল, অব্বেল গিদাল, হাছেন গিদাল, ছেফাতুল্যা, ওসমান গিদাল, আব্দুল হামিদ, রফিস দোহার, দোরার আবু বক্কর উল্লেখ যোগ্য।
পুঁথির শিল্পীদর মধ্যে সোলায়মান, খলিল, হাছেন আলী আরও অনেকেই পুঁথি পাঠ করে এলাকার মানুষকে বিমোহিত করত। সত্যপীর, বাহারাম বাদশা, ইউসুফ জুলেখা, দেলদার কুমার, দেল পিঞ্জির, হাতেম তাই, সেকেন্দার বাদশা আরও অনেক নামের পুঁথি পাঠের আসর হত। শুকনো মৌসুমের সময় জোসনা রাতে এসব পুঁথি পাঠের আসব জমে উঠতো।
ধুয়া গান (লেটো গান), জঙ্গনামা, পদ্মপুরান, কুশান গান, কবিয়াল গানের উল্লেখ যোগ্য শিল্পি এলাকার জনগণকে বিনোদন দিত।
এখনো ভাওয়াইয়া গানের জন্য ভূরুঙ্গামারীর শিল্পীদের জনপ্রিয়তা। মজিদুল ইসলাম খোকন, আব্দুল মালেক, আসমা, মল্লিকা আরো অনেক শিল্পী বেশ সুনাম রয়েছে।
এখনো পাইকের ছড়াসহ উপজেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় পদ্মপুরান গানের আসর বসতে দেখা যায়।নাট্য চর্চার প্রচলন কমে গেলেও বিলুপ্ত হয়নি। প্রতি বছর সপ্তাহব্যাপী ভরতের Star (পাটেশ্বরী) ও বারনী মেলা (কালিরহাট), তাজিয়া মেলা (ডিপের হাট)এ আয়োজন হতো। এখন নিয়মিত ভাবে এসব মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।
এ মেলা গুলোতে প্রচুর লোকজনের সমাগম হত।দুর-দুরান্ত থেকে এসব মেলা দেখতে আসত। উপজেলার কবি নজরুল ইসলাম শিল্পকলা একাডেমি ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতা দিবস,বিজয় দিবস,বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন পার্বণে নাটক ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব ছাড়া কীর্তন, মারফতী, ভজন সংগিতের প্রচলন রয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধ:
উপজেলায় তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা-৯৩০জন। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা-৮১০ জন। ২৩শে মার্চ ভূরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ, আনসার-মুজাহিদ, সাবেক ইপিআর, আওয়ামীলীগ কর্মী, নেতা এবং সর্বস্তরের জনগণের এক বিরাট সমাবেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।
ঐ সমাবেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভূরুঙ্গামারীর ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।
২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু হলে ২৬শে মার্চ জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় নেতাদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং সমস্ত ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করা হয়।
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মোতাবেক সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্যও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।
ইতোমধ্যে ভূরুঙ্গামারী থানার সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলোর সাবেক অবাঙ্গালী ইপিআর-রা সাবেক বাঙ্গালী ইপিআর-দের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ইপিআর আনিস মোল্লা এবং রওশনুল বারীর নেতৃত্বে ইপিআররের সদস্যবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা কামনা করলে স্থানীয় এক জরুরী বৈঠকে অবাঙ্গালী ইপিআরদের সক্রিয় সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
২৮শে মার্চ অবাঙ্গালী ইপিআরদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরদিন ২৯ মার্চ বাঙ্গালী ইপিআর এবং সম্মিলিত ছাত্র জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জয়মনিরহাট ক্যাম্পের একজন অবাঙ্গালী সুবেদার, একজন ড্রাইভার এবং একজন ওয়্যারলেস অপারেটর নিহত হয়।
উক্ত জয়মনিরহাট ক্যাম্পে অবাঙ্গালী ইপিআরদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী জয়মনিরহাটের একজন অবাঙ্গালী চক্ষু চিকিৎসক জনগণের হাতে নিহত হয়।
অত্র থানার অন্যান্য সীমান্ত ফাঁড়ি যেমন- কেদার, সোনাহাট, ধলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী ইপিআরদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন অবাঙ্গালী ইপিআর নিহত হয়।
অবাঙ্গালী ইপিআরদের কবল থেকে জয়মনিরহাট ক্যাম্প ও অস্ত্রাদি উদ্ধার করা হয় এবং নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী থানার সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরগণকে তাদের অস্ত্রসমেত উক্ত ক্যাম্পে জরুরী ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়।
অতঃপর সাবেক বাঙ্গালী ইপিআরগণের সঙ্গে আনসার, মুজাহিদ এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জয়মনিরহাটে যোগ দেয়। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ও এখানে যোগ দেয়। এদের সকলকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়ে হানাদার বাহিনী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়।
জয়মনিরহাটে সংঘবদ্ধ এই দলকে বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং পুলিশ ফাঁড়ি থেকে প্রাপ্ত সামান্য অস্ত্র দিয়েই রংপুর সামরিক গ্যারিসন থেকে হানাদার বাহিনী যাতে অত্র অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিস্তাপুল প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠানো হয়।
২৯শে মার্চ শামছুল হক চৌধুরী ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জ সীমান্ত ঘাঁটির সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের অনুরোধে উক্ত সেনাধ্যক্ষ প্রাথমিক বেসরকারী সাহায্য হিসেবে ১লা এপ্রিল মধ্যরাতে ২টি হাল্কা মেশিনগান, কিছুসংখ্যক রাইফেল এবং প্রচুর হাতবোমা প্রদান করেন।
এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ তিস্তাপ্রতিরোধ কেন্দ্রে সরাসরি পাঠানো হয়। পরবর্তীতে সোনাহাট ও সাহেবগঞ্জের ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি থেকে আরও সামরিক সাহায্য নেওয়া হয়।৫ই এপ্রিল ভূরুঙ্গামারী কলেজে প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। যুবক এবং ছাত্ররা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র-যুবক এখানে আসতে থাকলে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা হয়।
সমগ্র রংপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাঙ্গালী ইপিআরদেরকে ভূরুঙ্গামারী থানায় সংঘবদ্ধ করে দুই কোম্পানি ইপিআরকে তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠান হয় এবং এক কোম্পানী ইপিআরকে ভূরুঙ্গামারীতে সংরক্ষিত রাখা হয়।
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ও প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ভূরুঙ্গামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হানাদার কবলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা তৈরি করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়েই গেরিলাদেরকে সরাসরি প্রতিরোধ ঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে।
পরবর্তীকালে এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে অত্র থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেছেন।
এছাড়া ভারতীয় জনগণ ভূরুঙ্গামারী থানার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাল, গম, আলু, কেরোসিন, পেট্রোল, বিস্কুট, কাপড়, ঔষধপত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন। ভারতে প্রবেশের পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করা হয়।
ভারতের পশ্চিম বাংলা সীমান্তের সাহেবগঞ্জ ও আসামের সোনাহাটে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনুমোদনে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা অধিকৃত ভূরুঙ্গামারী এবং নাগেশ্বরী থানার বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের প্রতি আঘাত হানতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করার জন্য পশ্চিম বাংলা সীমান্তে যুবশিবির খোলার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
প্রাথমিক অবস্থায় এই যুবশিবিরগুলো স্থানীয় ভারতীয় জনগনের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ছিল।
পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার যুবশিবিরগুলোর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুবশিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর তাদের উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে পাঠানো হতো।
দুধকুমার নদীর পূর্বতীরস্থ এবং ভূরুঙ্গামারী থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদার কবল মুক্ত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের সার্বিক সাহায্যের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি।
মুক্তাঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার জন্য নাগেশ্বরী থানার সুবলপাড় বন্দরে এবং মাদারগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের সাবেক ইপিআর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ-এর অধীনস্থ সাহেবগঞ্জ ঘাঁটির গেরিলাযোদ্ধা এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আসাম সীমান্তের সোনাহাট গাঁটির গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যদের এক যৌথ অভিযানের পর ১৭ই নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী মুক্ত হয়।
এর পরপরই অত্র থানার আন্ধারীঝাড় বাজার থেকে পাক বাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে পিছু হটে গেলে ভূরুঙ্গামারী থানা শত্রুমুক্ত হয়। এই এলাকা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আশ্রিত জনগণ বিধ্বস্ত ভূরুঙ্গামারীতে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে।
মাতৃভুমিতে পা দিয়েই জনগণের আনন্দ-উল্লাস সবাইকে অভিভূত করে। ডিসেম্বরে সারা বাংলাদেশের মুক্তির সাথে সাথে জনগণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে উল্লাসিত হয়েছে।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন:
গণকবর ১টি (টিএনও বাসভবনের পেছনে গণকবর);
বধ্যভূমি ১টি (হাসপাতালের পেছনে);এ ছাড়া ভুরুঙ্গামারী ইউনিয়নের বাগভান্ডার গ্রামে ৩০-৩২টি মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে।
প্রধান নদী:
দুধকুমার, ফুলকুমার,শংকোশ।
বিল ও জলাশয়:
প্রতি বছর দুধকুমার,শংকোশ,ফুলকুমরের ভাঙ্গনে নদীর গতিপথ পরির্তন হয়। নদীর এসব পুরাতন গতিপথ বিল ও জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। দিয়াডাঙ্গা বিল, সর্বজায়া বিল ও মরা শংকোশ বিল, সোনাহাট ছড়া, পাটেশ্বরী ছড়া, আবেদের কোলা, বহলগুড়ি ছড়া উল্লেখযোগ্য।
দর্শণীয় ও প্রসিদ্ধ স্থান:
-
- মীর জুমলা প্রাচীন মসজিদ
- পাটেশ্বরী/সোনাহাট ব্রিজ।
- সোনাহাট স্থলবন্দর ।
- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর বাড়ি।
- জয়মনির হাট শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি।
- জয়মনিরহাট জমিদার বাড়ি।
- জয়মনিরহাট জামে মসজিদ।
- সোনাহাট কলেজ।
- বাগভান্ডার সুইচ গেইট।
- বগনির পাড় জামে মসজিদ।
- দেওয়ানের খামার জামে মসজিদ।
- প্রেম ব্রিজ
- সুনিলের কুড়া
- লাল পুল
- সোনাহাট কাঠের ব্রীজ
- বৃটিশ রেল লাইন ( বর্তমানে পরিত্যাক্ত)
- সোনাহাট কালী মন্দির
বিবিধ
- মসজিদ: ৩৪১টি
- মন্দির: ১৪টি
- গীর্জা: ১টি
- পাবলিক লাইব্রেরী: ১টি
- পাঠাগার: ১টি
- প্রেস ক্লাব: ১টি
- তফশীল অফিস: ১০টি
- কমিউনিটি সেন্টার: ৮টি
- সিনেমা হল: নাই(উল্লেখ্য যে গত কয়েক বছর আগেও ৩ টি সিনেমা হল ছিলো।)
- ডাকবাংলো: ১টি
- রেষ্টহাউজ:৫টি
- হাটবাজার:২৫টি
- ভরতের মেলা (পাটেশ্বরী) ও বারনী মেলা (কালিরহাট),তাজিয়া মেলা (ডিপের হাট) উল্লেখযোগ্য।(বর্তমানে নিয়মিত ভাবে এসব মেলা অনুষ্ঠিত হয় না।)
- দ্রুত সুবিধা প্রাপ্ত মৌজা: ২৭টি(আংশিক)
- এনজিও: ১৪টি
- সমাজকল্যাণ সংখ্যা: ২৩টি
- এতিমখানার সংখ্যা: ৯টি

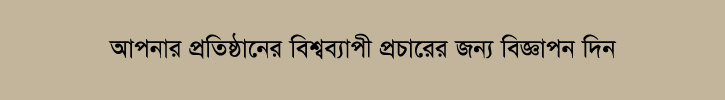










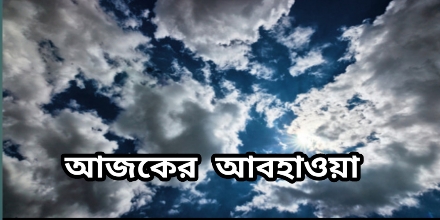

























[…] ১৯৫৪ইং মুসলীমলীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির সংগঠক, কুড়িগ্রাম। পড়ুন>>ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সকল তথ্যাবলী […]
Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted
to write a little comment to support you.
Feel free to visit my web page … বিকাশে অটো টাকা কাটা